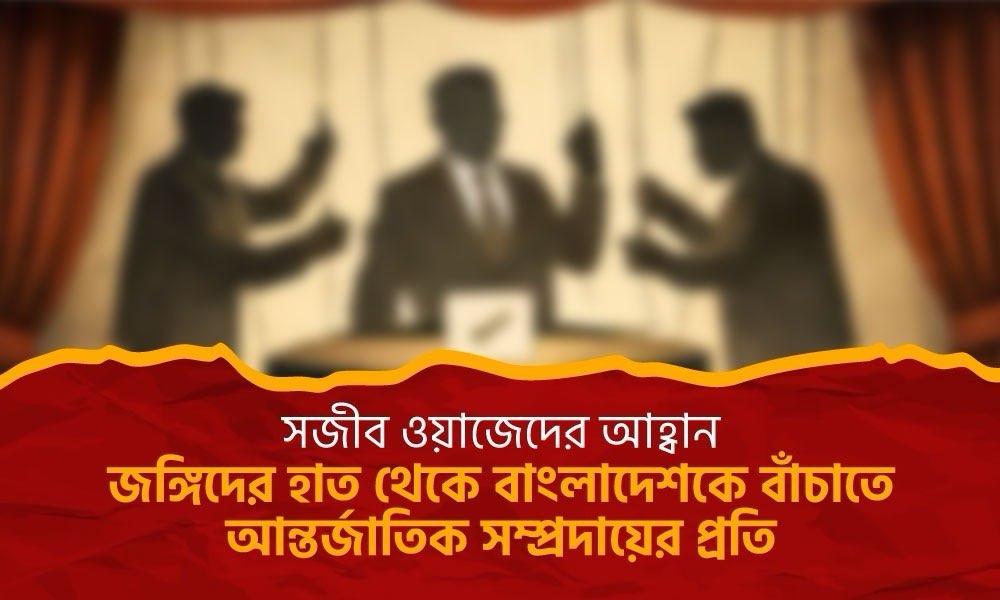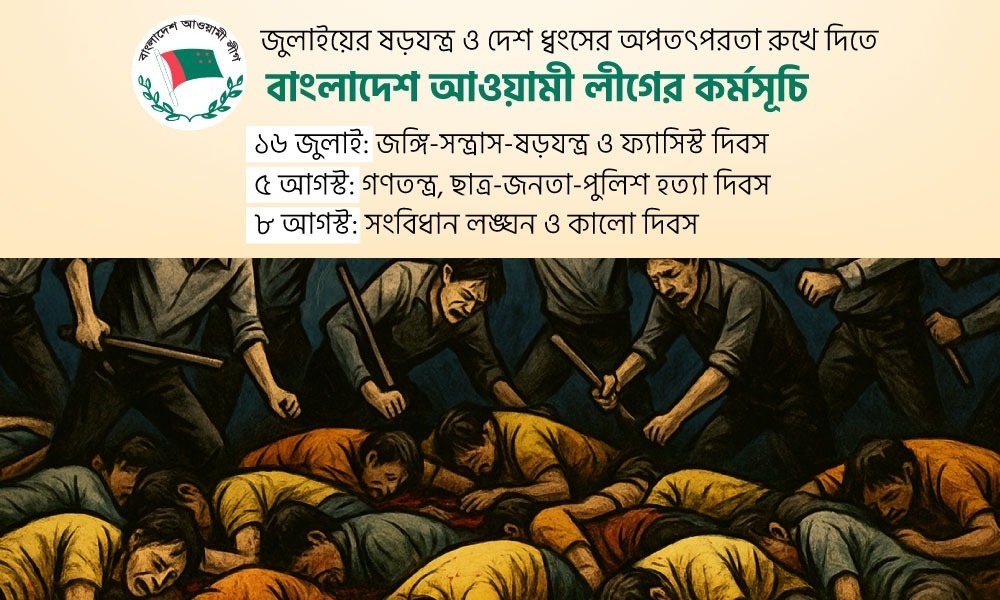মুনতাসীর মামুনঃ
‘অসহযোগ’ ও ‘অহিংসা’- এ দুটি প্রত্যয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিকভাবে এ দুটি প্রত্যয় আগে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা জানা যায় না, অসহযোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে থেকে পারে, অহিংসা নয়। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ ব্যবহার করেছেন রাজনীতিতে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত, তবে অসহযোগের ভিত্তি সবসময় রাখতে চেয়েছেন অহিংস। শেষোক্ত প্রত্যয়টির উদ্ভব তার ধর্ম বিশ্বাস থেকে। তিনি জৈনধর্ম বিশ্বাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ ধর্মে কোনো জীবহত্যা অধর্ম। অহিংসা প্রত্যয়টি তিনি প্রথম ব্যবহার করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। শাসক অত্যাচার করবে সেটির প্রতিবাদ সহিংস হবে না, নির্যাতন সহ্য করে এর অসারতা প্রমাণ করতে হবে। যিশুর বাণীও তা-ই ছিল। গান্ধীজির মতে, ‘অহিংসার অর্থ অন্যায়কারীর নিকট নতি স্বীকার নয়। অহিংসার অর্থ স্বৈরাচারী ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সমগ্র আত্মার বোধকে উত্থিত করা।’
গান্ধীজি দু’টি প্রত্যয়কেই রাজনীতিতে একইসঙ্গে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, এককভাবে একটিকে নয়। তিনি এতে পুরোপুরি সফল হননি। তবে, প্রত্যয় দু’টিকে রাজনীতিতে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন। এই প্রত্যয় পাশ্চাত্যে হাসিঠাট্টার বিষয় হলেও অগ্রাহ্য করেননি কেউ, তবে সফলতা নিয়ে হয়তো সংশয় ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী এ প্রত্যয়ের উদ্ভাবন করেন, নেলসন ম্যান্ডেলাও তা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবে, প্রত্যয় দু’টি একজনই সফলভাবে ব্যবহার করেছেন এবং এই উপমহাদেশেই। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশে যিনি পরিচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা শুধু বঙ্গবন্ধু নামে।
এখানে দু’জনের তুলনামূলক আলোচনা নয় এবং করা উচিতও নয়, কেননা দু’জনের সময় আলাদা। গান্ধীজি যখন প্রত্যয় দুটির উদ্ভাবন করেন তখন বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে মাত্র। অসহযোগ আন্দোলনের ঠিক ৫০ বছর পর বঙ্গবন্ধু তা প্রয়োগ করে সফল করেন। তখন পৃথিবী বদলে গেছে। এখানে বরং বোঝার চেষ্টা করব, যিনি প্রত্যয় দু’টির উদ্ভাবক, তিনি কেন সফল হলেন না। সফল হলেন তিনি, যিনি এই প্রত্যয় উদ্ভাবনের ৫০ বছর পর তা ব্যবহার করেন। গান্ধীর রাজনীতিতে তিনি বড় হয়েছিলেন এবং মহাত্মাকে শ্রদ্ধাও করতেন। কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পর বেলেঘাটায় গান্ধীজি অবস্থান করছেন। তখনকার এক চিত্রে দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দী গেছেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে আছেন তরুণ একহারা শেখ মুজিবুর রহমান।
তবে, বঙ্গবন্ধুর প্রিয় ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এ কারণে বোধহয়, তিনি অহিংস অসহযোগের আন্দোলন করার পক্ষপাতী হলেও, এটি মনে রেখেছেন, শাসকের বিরুদ্ধে যদি তা কার্যকর না হয়, তাহলে সুভাষ চন্দ্রের অনুসারী হবেন তিনি। গান্ধীজির চিন্তায় তেমন পরিকল্পনার কোনো স্থান ছিল না। সুভাষচন্দ্রকে তিনি পছন্দও করতেন না।
গান্ধীজি কংগ্রেসে যোগ দেন ১৯১৪ সালে। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির তখন ধারক-বাহক কংগ্রেস। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিওয়ানবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটান ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার। এই অকথ্য হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার তদন্তে হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। হান্টার কমিশন ১৯২০ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে ডায়ার বা তার সহযোগীদের দায়ী করা হয়নি। অন্যদিকে একই সময়ে তুরস্কেও খিলাফতের অবসান ঘটে।
খিলাফত কমিটি ১ ও ২ জুন ১৯২০ সালে এক সম্মেলন আহ্বান করে এসব ঘটনা (প্রধানত খিলাফত) নিয়ে আলোচনার জন্য। এখানে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলমানরা হিন্দু সম্প্রদায়কে সহযোগিতার আহ্বান জানান; কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এতে সায় দেয়নি। গান্ধী এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১ আগস্ট ভারতে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গান্ধীর নেতৃত্বে হরতাল ঘোষণা করে। গান্ধী সরকার থেকে যেসব মেডেল পেয়েছিলেন তা ফেরত দেন এবং বড়লাটকে জানান, ‘‘আমার মুসলমান ভাইগণের ধর্ম বিশ্বাসে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা দূর না হওয়া পর্যন্ত এসব ‘মেডেল’ ব্যবহার করিতে আমার বিবেকে বাধে। সুতরাং, আজ হইতে খিলাফত আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার নির্দেশে আমি মেডেলগুলি ফেরত পাঠাইলাম।’’ এর আরেকটি কারণ হিসেবে গান্ধী জালিয়ানওয়ালবাগের ঘটনারও উল্লেখ করেন। অসহযোগের সূত্রপাত এখানেই।
১৯২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয় কলকাতায়। লালা লাজপত রায় এতে সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় যেসব অন্যায় সাধিত হয়েছে তার প্রতিবিধান এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া গতি নেই। এ অসহযোগিতার ভিত্তি চারটি -
১. সরকার প্রদত্ত সব উপাধি, সামাজিক পদ ও স্থানীয় সরকারের পদ থেকে পদত্যাগ, ২. সরকারি দরবার বা সরকারি সম্মান আয়োজন বর্জন, ৩. সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন ও ‘জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন
৪. আদালত বর্জন ও সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা, ৫. ইরাকে সামরিক-বেসামরিক পদে চাকরি অস্বীকার, ৬. বিধান পরিষদের নির্বাচন বর্জন, যারা বর্জন করবে না তাদের ভোট না দেয়া এবং ৭. বিদেশি দ্রব্য বর্জন বা বয়কট।
অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর পটভূমি তৈরি করেছিল ১৯০০ থেকে শুরু হওয়া ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলন। বাংলায় এ আন্দোলন ব্যাপকতা অর্জন করে বিশেষ করে বয়কট, পরে তা মাদক পণ্য বয়কট পর্যন্ত পৌঁছায়। ছাত্রদের অনেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘জাতীয়’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রচুর আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলন ক্রমেই র্যাডিকাল আন্দোলনের দিকে যেতে থাকে গান্ধী যা পছন্দ করেননি। আহমদাবাদ কংগ্রেসে এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মোহানী পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব করলে গান্ধী ক্ষুব্ধ হন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা গ্রামে কৃষক পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে থানায় আগুন দেয়। ২২ জন পুলিশের মৃত্যু হয়। এ সংবাদ শুনে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।
১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য করার মাধ্যমে আবার অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং সরকার একইভাবে তা দমন করে। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার ২৭ বছর পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে অজস্র রক্তপাত ও ক্ষোভের মাধ্যমে।
‘গান্ধীজি’- লিখেছেন সরদার ফজলুল করিম, ‘ছিলেন প্রধানত ভারতের রক্ষণশীল সমাজ এবং প্রতিষ্ঠাকামী ধনিক শ্রেণির প্রতিভূ। এ শ্রেণি নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষকের জঙ্গি চেতনা এবং সংগঠনকে ভয়ের চোখে দেখত। এ ভীতি থেকে জনতা অধিকতর সংগ্রামী হতে চাইলে নেতৃত্ব তার রাশ টেনে ধরতে চেয়েছে। আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ব্যাপক জনতাকে অনুপ্রাণিত করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল গান্ধীজির। হিন্দু সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষ তাকে সাধু পুরুষের মতো ভক্তি করত। ফলে তার পরিচালনায় এ আন্দোলন পূর্বেকার সব আন্দোলনকে অতিক্রম করে এক ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।’ গান্ধীজি সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছেন, হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বেরও আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার। তাই রাজনৈতিক দিক নয়, সামাজিকভাবেও এবং তার সরল জীবনযাপন সাধারণের কাছে তাকে ‘মহাত্মা’য় পরিণত করেছিল। শুধু হিন্দু নয়, ভারতের সব ধর্মের মানুষের কাছেই তিনি কম-বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার পর তার উপাধি হয় ভারতের জাতির পিতা। ১৯৪৮ সালে আরএসএসের নাথুরাম গডসে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। ১৯৭৫ সালে দু’কন্যা ব্যতীত সপরিবারে তিনি নিহত হন।
বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি আমাদের জেনারেশনের সবার জানা। কলকাতার রাজনীতি থেকে তিনি ভারত বিভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও পূর্ববঙ্গবাসীর ছিল, বলা চলে বেশি ছিল। ১৯৪৭ সালের পর ঔপনিবেশিক কাঠামো অটুট রেখেও ভারতীয় রাজনীতিবিদরা নিজেদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। সেখানে ডান-বাম বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত ছিল, তবে তা নিরসনের উপায়ও নিহিত ছিল গণতান্ত্রিক কাঠামোয়। অন্যদিকে, পাকিস্তান হলেও পশ্চিম পাকিস্তান বা কেন্দ্রীয় শাসকরা ব্রিটিশ কাঠামোর ওপর পাকিস্তান ঔপনিবেশিক কাঠামো চাপিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক আবরণ ১৯৫৮ পর্যন্ত থাকলেও গণতান্ত্রিক অধিকার বাঙালি কখনও প্রযোগ করতে পারেনি; কিন্তু এটিও সত্য, মুসলমানত্ব ও পাকিস্তানবাদ সহজে বাঙালির মন থেকে একেবারে উপড়ে ফেলা যায়নি, এখনও। এ সমস্যা ভারতে ১৯৪৭-এর পর হয়নি, এখন হচ্ছে। যারা পাকিস্তান রাজনীতি করেছিলেন তারা ঢাকায় এসে অনুধাবন করলেন, তারা ভুল রাজনীতি করছেন। তখন তারা সে রাজনীতি থেকে সরে আসতে থাকেন, বিশেষ করে তরুণরা। তখন ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী প্রমুখের প্রভাব সত্ত্বেও তরুণরাও নিজেদের প্লাটফরম গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার বয়স যখন ২৮ থেকে ৩০-এর মধ্যে তখনই তিনি নেতা হিসেবে পরিচিত এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি-ই সবসময় গোয়েন্দাদের সতর্ক নজরে থেকেছেন এবং লিয়াকত আলী খান তখনই আওয়ামী লীগকে দেশের শত্রু ঘোষণা করেছিলেন। ওই ধারণা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনও সরে যেতে পারেনি। কংগ্রেস শুরু করেছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি এবং ৫০ বছর ধরে সে রাজনীতির চর্চা করে এসেছে; কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে সেই আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি করা সম্ভব হয়নি। শুরু থেকেই সংঘাতের পথে যেতে হয়েছে। সেজন্য সেসময়কার তরুণ নেতৃত্ব অহিংস গণতান্ত্রিক পন্থায় আস্থা রেখেও বিকল্পের পথ খোলা রেখেছিলেন। গান্ধীজির মতো বিকল্প পথ রুদ্ধ করে দেননি। বঙ্গবন্ধুকে অন্নদাশঙ্কর রায় প্রশ্ন করেছিলেন, ‘বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এল।’ ‘শুনবেন?’ তিনি [মুজিব] মুচকি হেসে বললেন, সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরাবর্দী [সোহরাওয়ার্দী] সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির একদেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারত। সারা জগৎ জয় করতে পারত। They could conquer the world. বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বললেন, ‘দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাদের প্রস্তাবে। তারা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা। সে স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এ আমার চিন্তা। হবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল। বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা, কেউ বলে পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি স্লোগান দিই জয় বাংলা। তখন ওরা বিদ্রূপ করে বলে, জয় বাংলা না জয় মা কালী! কী অপমান! সে অপমান আমি সেদিন হজম করি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয় যা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।’
সেই থেকে শুরু। দীর্ঘ ২৫ বছর গান্ধীজির মতোই জেল-জুলুম সয়েছেন তবে গান্ধীর মতো অনশনকে কখনও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি। গান্ধীজিকে স্বাধীনতার আহ্বান জানাতে অনেক সময় লেগেছে। তার বহু আগেই বিপ্লবীরা স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শুরু থেকেই বাংলাদেশের কথা ভেবেছেন এবং পাকিস্তান হওয়ার ১৫ বছরের মাথায় প্রবাসী সরকার গঠন করে স্বাধীন বাংলার লড়াই করতে চেয়েছেন ১৯৬২ সালে। সুভাষ বসু যেমন, স্বাধীনতার জন্য বিদেশি শক্তির সাহায্য চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধুও তেমনি সহায়তার জন্য জওহরলাল নেহেরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত আবেদন জানিয়েছেন এবং সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন। বাস্তবতা হল, বাংলাদেশের চারদিকে ভারত এবং ভারত ছাড়া আর কারও কাছে সাহায্য চাওয়া সম্ভব ছিল না; কিন্তু ছিল চরম সাহসের ব্যাপার। কারণ বিষয়টি ছিল মুসলমানত্ব ও পাকিস্তানবাদের বিপরীত।
১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো রাজনীতিক নেতা ছিলেন না [হতে পারেননি]। তিনিই মানস জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। গান্ধীজির প্রতিদ্বন্দ্বী, তার মাপের নেতা ভারতে ছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন ১৯২০-এর মধ্যে এবং ১৯৩০-এর মধ্যে ভারতের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানস জগতে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।
আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কারণে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। আওয়ামী লীগ ১৫ মার্চে ২৬টি নির্দেশনা দিয়ে তা বিধিবদ্ধ ও আনুষ্ঠানিক করে তোলে।
১ মার্চ ১৯৭১ সালে, ইয়াহিয়া খান সংসদ স্থগিত করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় মিছিলের ঢল নামে এবং সবাই পূর্বাণী হোটেলের দিকে এগোতে থাকে যেখানে বঙ্গবন্ধু সভা করছিলেন সহযোগীদের সঙ্গে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্লোগান দেয়া হয়- ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা’, ‘জাগো জাগো বাঙালি জাগো’। স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগানই নির্ধারণ করে দেয় বাঙালি কী চায় এবং সেই দাবি আদায়ের জন্য মানসিকভাবে সে প্রস্তুত। ১৯৬৯ সালে এ স্লোগানগুলোর উদ্ভব এবং বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সাধারণকে উজ্জীবিত ও শাণিত এবং প্রস্তুত করে তুলতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন এবং পরপর দু’দিন হরতাল আহ্বান করেন ও জানান ৭ মার্চ তিনি তার অভিপ্রায় জানাবেন জনসভার মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, সেদিনই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ করার নির্দেশ দেন। সরকার কারফিউ জারি করে, জনতা তা ভাঙার চেষ্টা করে গুলি খায়। উল্লেখ্য, ২৫ মার্চের আগে নিরস্ত্র মানুষ সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেনি এবং যুদ্ধের ঘোষণাও দেয়নি।
২ মার্চ বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দেন অসহযোগ আন্দোলন হবে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে তা এগিয়ে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাধে। ঘোষণা করেন, ‘এখানে বসবাসকারী বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই সমান। সবাই আমাদের ভাই’ এবং সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৭ মার্চের অমর বক্তৃতার কথা আর নতুন করে বলতে চাই না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাঝেও বিকল্প সশস্ত্র পথের ইঙ্গিত তিনি রেখেছিলেন, প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন এবং সব শেষে ঘোষণা করেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীন তার সংগ্রাম।’ এরকম জোরালোভাবে কোনো নেতা, যিনি সশস্ত্র পন্থায় বিশ্বাসী নন, জনগণের সব শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কথা বলেননি। গান্ধীজিও নয়, এমনকি স্বাধীনতার ডাক দিতেও অসহযোগে কুণ্ঠিত ছিলেন।
গান্ধীজির নয়, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর যে মন্তব্য করেছেন, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ নিয়ে এর বাইরে বলার তেমন কিছু নেই। লিখেছেন তিনি-‘অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখর। এ আন্দোলন একইসঙ্গে সিভিল সমাজের সব অংশ, স্তর, শ্রেণি, পেশা, নারী-পুরুষ এবং রাষ্ট্রের অংশ প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পুলিশ, ইপিআর এবং গোপনে সামরিক বাহিনীর বাঙালি ইউনিট অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যুক্ততার মধ্য দিয়ে তৈরি করেছে রূপান্তরিত এক জাতিসত্তা এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা। সাধারণ মানুষ যদি সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা করে, তাহলে এ সরকার বাতাসে পাতার মতো উড়ে যায় এবং রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটে।’
১৪ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ অসহযোগে জনগণের করণীয় সম্পর্কে ৩৫টি নির্দেশ প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের পক্ষে। ২ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ যেসব বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট :
১. সাধারণকে আন্দোলনে উজ্জীবিত রাখা, ২. কেন্দ্রের সঙ্গে অসহযোগ ৩. ‘প্রদেশ’ পর্যায়ে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করা যাতে সাধারণ বিপদগ্রস্ত বা বিরূপ হয়।
যেমন ৩ থেকে ৬ মার্চ বলা হল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল। সব বন্ধ থাকবে শুধু অ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্র সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি পরিবহন হরতালমুক্ত থাকবে। ২টার পর সব কাজ আবার স্বাভাবিক। ৭ মার্চ, পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকেই তিনি প্রতিরোধ [গেরিলা কার্যক্রম] ও স্বাধীনতার ডাক দেন; কিন্তু তাত্ত্বিক বা বাস্তব থেকে দেখলেও বলা সম্ভব ছিল না যে, তিনি ‘দেশদ্রোহমূলক’ বক্তব্য রেখেছেন। ভারতে যারা অসহযোগ আন্দোলন করেছেন তারা কখনও এ ধরনের বক্তব্য রাখতে পারেননি। ১১ মার্চ থেকে দেখি সরকারি-বেসরকারি ভবনে বাংলাদেশেরও কালো পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে। ১২ তারিখ তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে সেনাবাহিনীকে কোনো জ্বালানি সরবরাহ না করতে। এ সময় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলি, লাঠিচার্জ, হুমকি সবই অব্যাহত ছিল। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন; কিন্তু সশস্ত্র পথে যাননি। অহিংস অসহযোগ করেছেন। যখন দেখেছেন আর সম্ভব নয় তখন সশস্ত্র প্রতিরোধে গেছেন এবং তা বৈধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন-
‘পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে সর্বাত্মক অসহযোগকে গণঅভ্যুত্থানের স্ট্র্যাটেজি হিসেবে বাছাই করে। সরকার ও রাষ্ট্রকে অচল করে রাষ্ট্রশক্তির পতন সংঘটিত করার স্ট্র্যাটেজির ঐতিহ্য এসেছে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে। এ ঐতিহ্য থেকে সাধারণ মানুষ তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। প্রথম শিক্ষা হচ্ছে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি দিয়ে ঔপনিবেশিকতা থেকে উদ্ধার সম্ভব নয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে, সর্বাত্মক অসহযোগের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের বোধ সক্রিয় রাখা। তৃতীয় শিক্ষা হচ্ছে এ সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্থায়ী সংলাপের ব্যবস্থা তৈরি করা।’
অসহযোগের যে ৩৫টি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা হল নিরস্ত্র মানুষের কর্তৃত্ব। পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিল একেবারে নতুন ধারণা। সাধারণ মানুষ নির্বাচিত করেছেন জনপ্রতিনিধিদের। জনপ্রতিনিধিরা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তা সমগ্র জনসাধারণ মানছে। এর বাইরে নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মচারীরা এই নৈতিক জোরের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি কিন্তু ক্ষমতায় যাননি তাদের কথা-ই মানতে বাধ্য হচ্ছেন। এ কর্তৃত্বের স্বাদ বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো নিরস্ত্রকে দিতে পেরেছিলেন, যে কারণে তারা ছিল উদ্বুদ্ধ।
ভারতে অসহযোগ আন্দোলন কোনো পরিণতি পায়নি। বাংলাদেশে পেয়েছে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে অহিংস অসহযোগের শেষ হয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ স্বাধীনতার ডাক বৈধতা পেয়েছিল এ কারণে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা নির্বাচনে জিতেছিল এবং তাদের ক্ষমতা না দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিরা বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে। বাঙালি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ দ্বন্দ্বের সমাধান চেয়েছে এবং এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।
আমি শুরুতেই টাইম ফ্রেম বা সময়কালের কথা উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সফল হওয়ার অনূকুল কিছু উপাদান ছিল। দেশটি ছোট, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা এক, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে পঁচিশ বছর এবং অন্তিমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ প্রধান দল ও বঙ্গবন্ধু জাতীয় ঐক্য ও স্বপ্নের প্রতীকে পরিণত হন। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর তিনিই ছিলেন একমাত্র জাতীয় নেতা যার ডাকে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং যে কোনো আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিল। এমনকি বাঙালি কর্মচারীরাও কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ মানতে রাজি হয়নি যা ছিল অভূতপূর্ব। অসহযোগের ৩৫টি নির্দেশ সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল এবং এর কৌশল ছিল আন্দোলন; কিন্তু দৈনন্দিন কার্য চালিয়ে যাওয়ার স্পেস। এটি খুবই জরুরি। বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশ যখন সবাই মানা শুরু করলেন, তখনই কিন্তু পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে সমান্তরালভাবে আলাদা রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি হল। এটি পৃথিবীর কোথাও হয়নি।
পক্ষান্তরে, ভারত ১৯২০-৩০ সালে প্রায় এক মহাদেশ। ভাষা হাজারের ওপর। হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন বর্ণ-গোত্রে বিভক্ত, মুসলমানদের মধ্যে ‘আশরাফ’ ‘আতরাফ’ দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় বিভেদ ও স্বার্থ বিরাজ করছিল। দেশীয় রাজ্য ছিল অনেক। সরকারের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীও সরকার পক্ষ ত্যাগ করেনি [ব্যতিক্রম কিছু ছিল] বরং প্রচণ্ড নিপীড়ন চালিয়েছে। অর্থাৎ মহাত্মার প্রতিও তারা পূর্ণ আস্থা রাখেননি এবং অসহযোগের মূল লক্ষ নিয়েও কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ধনী, কৃষক, মজুরদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এ পরিস্থিতিতে অসহযোগ চালিয়ে যাওয়া দীর্ঘদিন সম্ভব ছিল না।
মহাত্মা গান্ধীর কৃতিত্ব এই যে, অসহযোগ অহিংস আন্দোলনকে তিনি একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় হিসেবে নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। তার এই আন্দোলন কংগ্রেস কর্মীদের ছাড়া, রাজনীতির বাইরের মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের শিক্ষা প্রজ্বলিত করেছিল। তার জীবনচর্যা ও রাজনীতির মধ্যে তিনি তফাৎ কমিয়ে আনতে পেরেছিলেন, যেজন্য সবাই তাকে ‘মহাত্মা’ বলতেন। পৃথিবীর কোথাও সাধারণ মানুষ কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ‘মহাত্মা’ উপাধিতে ভূষিত করেনি। তার রাজনীতির সমর্থক না হলেও কেউ তাকে অসম্মান করার সাহস দেখাননি। কারণ তিনি ছিলেন সাধারণের মহাত্মা। অনেক সময় এ বোধের কারণে নিছক রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি বিবেচিত হননি। অহিংস অসহযোগ বললে গান্ধীজির কথাই মনে আসে কারণ ওই আন্দোলন জনমানসে নাড়া দিয়েছিল এবং তা তার নামের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে।
বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, পুরনো এই প্রত্যয়কে তিনি নবরূপ দিয়েছিলেন। তিনি আগে লক্ষ্য স্থির করেছেন এবং তারপর আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায় অসহযোগকে বেছে নিয়েছেন; কিন্তু অসহযোগ কার্যকর করার ও দীর্ঘদিন মানুষকে এ আন্দোলনে রাখার জন্য কী কী করতে হবে তাও বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি অহিংসার প্রতি জোর দিয়েছেন যাতে স্বাধীনতার ঘোষণাকে কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে। বিকল্প পন্থাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন এবং তা জনগণকে ইঙ্গিতে জানিয়েছেনও, যা বুঝতে মানুষের অসুবিধা হয়নি। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে সফলতার পথে নিয়ে গেছেন; কারণ সেই পথ বেয়েই মুক্তিযুদ্ধ করা গেছে। তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি মানুষের কাছে বন্ধুর মতো গেছেন, বঙ্গবন্ধু হয়ে গেছেন, বাংলার বন্ধু যিনি মানুষকে ছেড়ে যাবেন না। তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি অহিংস অসহযোগ কীভাবে সফল করতে হয় তার প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং ওই যে বিকল্প রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল, সে বিকল্প রাষ্ট্রে কোনো স্বৈরাচারী ধারণা ছিল না, দুর্নীতি ছিল না, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ছিল না, ছিল ভ্রাতৃত্ববোধ ও দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। এ ঐতিহ্য পরে মানুষকে সহায়তা করেছে ১৯৭৫-পরবর্তী স্বৈরশাসন উৎখাতে। বোরহানউদ্দিন খান যথার্থ লিখেছেন- ‘অসহযোগ আন্দোলনের বৈপ্লবিক চিন্তার একটি দিক হচ্ছে রাষ্ট্রকে সুরাষ্ট্রে পরিণত করে রাখা। যখনই সুরাষ্ট্র ব্যবস্থার বোধ থেকে, ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বাধীনতা ও সমতার বোধ থেকে স্খলিত হয়েছে, স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে, তখনই সাধারণ মানুষ সুরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা করেছে এবং গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটিয়েছে।’ আমরা মহাত্মা গান্ধীকে এখনও প্রাসঙ্গিক মনে করি, অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে এ কারণে যে, তিনি সশস্ত্রের ওপর নিরস্ত্রের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং সেটি ছিল আদর্শ, যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধারণ করেছেন এবং জীবন চর্চা, যার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত ও আদর্শের প্রতি সততা। বঙ্গবন্ধুরও ছিল তাই আর সাধারণ্যে তারা স্থান করে নিয়েছেন; এ কারণেই এবং সেজন্য দুজনই দুটি রাষ্ট্রের জাতির পিতা।